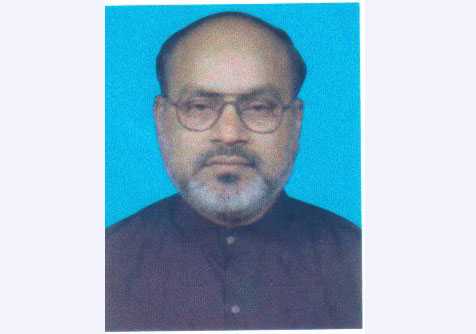
সুন্দরবনে তেলবাহী ট্যাংকারডুবির ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে গোটা দেশেই। তবে যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ততটা ক্ষতি হচ্ছে না বলে আশ্বস্ত করেছেন সরকার গঠিত তদন্ত কমিটি। এরই মধ্যে নদীতে ফিরে আসতে শুরু করেছে জলজ প্রাণী। পানিতে অক্সিজেনও পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত। কিন্তু জোয়ারের পানিতে ভেসে কিছু তেল ছড়িয়েছে নদীর তীর আর উদ্ভিদে। এর প্রভাব পড়তে পারে দীর্ঘমেয়াদি। এ নিয়ে মুখোমুখি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. দিদার-উল আলমের। তিনি জানিয়েছেন, কী হতে পারে, ভবিষ্যতে একই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে কী করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হাবিবুল্লাহ ফাহাদ
ট্যাংকারডুবির পর ফার্নেস অয়েল ছড়িয়ে পড়েছে সুন্দরবনে। পানিতে থাকা তেল অপসারণ হচ্ছে। কিন্তু কিছু তেল গাছ আর লতাগুল্মে জড়িয়ে গেছে। এর কী প্রভাব পড়তে পারে?
শ্বাস নেওয়ার জন্য যে শ্বাসমূল থাকে সেখানে তেল জড়িয়ে গেলে গাছের শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এতে গাছ মারাও যেতে পারে। বিশেষ করে পাতাসর্বস্ব গাছের ক্ষতি বেশি হয়।
হ্যাঁ, কিছু তেল অপসারণ হয়েছে, তবে চাইলেও পুরোপুরি তেল অপসারণ সম্ভব নয়। এখন যদি বৃষ্টি হয় তবে কিছুটা উপকার পাওয়া যাবে। গাছগুলোর প্রাকৃতিকভাবে গোসল হবে। যেটা কৃত্রিমভাবে করা যাবে না। বৃষ্টির জন্য পরবর্তী তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। এখন তো আর বৃষ্টি হবে না।
সরকার বলছে তেল প্রাণীকূলের খুব বেশি ক্ষতি হবে না
যে জায়গায় জাহাজ ডুবেছে সেখানকার উভচর প্রাণীর ক্ষতি হয়েছে। ডলফিন, কুমিরের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সুন্দরবনের মাটি, পানি ও গাছপালায় তেলগুলো এমনভাবে ছড়িয়েছে যে, এগুলো সহজে দূর করা সম্ভব নয়। ফার্নেস তেল বেশ আঠালো এবং ভারী। এগুলো সহজে সরে যায় না। মাটি ও গাছের শিকড়ের সঙ্গে লেগে আছে।
বন্যপ্রাণীর কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে?
বন্যপ্রাণীর গায়ে ফার্নেস তেল লাগলে তাদের গায়ের রঙ পাল্টে যাবে। তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। কোনো প্রাণী যদি ওই পানি পান করতে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে না, তবে ধীরে ধীরে ক্ষতি হবে। বিশেষ করে মাছের ব্যাপক ক্ষতি হবে। মাছ এই দূষিত পরিবেশে বাঁচতে পারবে না, মারা যাবে।
সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌরুট রাখায় বন্য পরিবেশের কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে?
সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌযান চলাচল করে এটা ঠিক নয়। নৌযানের জন্য তো বাইরে দিয়ে রাস্তা নেওয়ার কথা। এতে প্রতিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। শব্দের কারণে পশুপাখির অভয়াশ্রমে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইটের ভাটা সবই ধীরে ধীরে সুন্দরবনের দিকে এগোচ্ছে। সুন্দরবন যে শুধু বাংলাদেশের সম্পদ তা নয়, এটা বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে।
নৌ পরিবহন বিভাগ বলছে বনের ভেতর দিয়ে নৌরুট বন্ধ করা সম্ভব নয়...
বনের ভেতর দিয়ে কেন নৌযানের রাস্তা তৈরি হলো এটা তো আমি বুঝতে পারছি না? শ্যালা নদী দিয়ে কেন যেতে হবে? বলা আছে জরুরি প্রয়োজনে দিনে ১০ থেকে ১৫টি নৌযান ওই রুট দিয়ে চলাচল করতে পারবে। কিন্তু এখন তো দিনে ১৫০টির বেশি নৌযান ওই পথে চলাচল করছে।
নৌ-দুর্ঘটনা তো ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে
লঞ্চে মানুষ বহন করলে দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য থাকে বয়া। আর মালামাল বহন করলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি রাখতে হয়, যেন ডুবে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তেল যেন পানিতে না মেশে সেজন্য বিশেষ ধরনের পাউডার রয়েছে। যেগুলো পানিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এটি প্রয়োগ করলে তেল বেশিদূর ছড়াতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধে পানিতে ডুবে যাবে। এতে পানি দূষণজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা তো ছিল বলে মনে হয় না
আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। পরিকল্পনা হলেও তা কার্যকর হতে দেরি হয়। আসলে যারা নীতিনির্ধারক তাদের মধ্যেই সমস্যা আছে।
প্রাকৃতিক বনভূমি সংরক্ষণে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল?
একেকটি বনায়নের জন্য একেক ধরনের পদক্ষেপ জরুরি। যেমন সুন্দরবনের পরিবেশ পশুপাখির উপযোগী রাখার জন্য বনের ভেতর দিয়ে শব্দ করে এমন নৌযান চলাচল করতে দেওয়াই উচিত নয়। তবে পর্যটকদের জন্য নিয়ম মেনে নৌযান চলতে পারে। সেক্ষেত্রে তারাও যেন শব্দদূষণ অতিমাত্রায় না করেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
সুন্দরবন রক্ষায় আমাদের উদ্যোগের কি অভাব আছে?
সুন্দরবন রক্ষায় আমাদের যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার দরকার ছিল ততটুকু নিতে পারিনি। সুন্দরবন প্রকৃতির দান। এটিকে বাঁচানো এবং সুন্দর রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে।
সুন্দরবনের বাইরে থেকে তো এর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বোঝা যায় না
বাইরে থেকে তো ফিটফাট দেখা যায়, কিন্তু ভেতরে কী অবস্থা আমরা তা জানি না। সেখানে গাছ কেটে উজাড় করা হচ্ছে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে ক্ষতি হয় তা প্রাকৃতিকভাবেই নিরাময় হয়। বৃষ্টির মাধ্যমে গাছপালা সজীব হয়। মানুষ যা নিচ্ছে তা পূরণ হচ্ছে না।
সরকার কি কিছুই করছে না?
সরকারও করছে, কিন্তু রাজনৈতিক সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে খুব সময় লাগে। তার ওপর জনপ্রতিনিধি যাদের মাধ্যমে উন্নয়নটা হবে তাদের মধ্যেও সততার অভাব আছে। এ সবের কারণে সব কাজই দেরি হয়।
কী করা উচিত ছিল?
দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অনেক আগেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল। মানুষ সুশিক্ষিত হয়ে যতটুকু পেরেছে সক্ষমতা অর্জন করেছে।
প্রাকৃতিক বনভূমি তো আমাদের বড় সম্পদ...
কৃত্রিমভাবে বনায়ন সৃষ্টির চেয়ে প্রাকৃতিক বনায়নের পরিমাণ বেশি। কিন্তু প্রাকৃতিক বনায়ন রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে। বনায়নের ক্ষয়ক্ষতি হলে এটি পুষিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা দুর্বল। উল্টো নিজেদের স্বার্থের কারণেই মানুষ বনকে কলুষিত করছে। বন উজাড় করছে।
সুন্দরবনে তো নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে...
সুন্দরবনে নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এখানে অবশ্য জলদস্যু আছে। কিন্তু এগুলো তো এতদিনে থাকার কথা নয়। কারণ কোস্টগার্ড তো ওখানে সবসময় বিচরণ করে। আমাদের পাশেই ভারত। সুন্দরবনের ৪৫ শতাংশ তো তাদের। আমাদের ৫৫ শতাংশ। সবচেয়ে সুন্দর অংশটি বাংলাদেশের মধ্যেই। আমরা কিন্তু এগুলো ঠিকভাবে রাখতে পারছি না। ভারত কিন্তু তাদের অংশটি খুব ভালোভাবেই রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করে। ওরা সুসংগঠিত। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য অনেক কিছু করেছে।
সুন্দরবনে পর্যটক আকৃষ্ট করতে সরকার তো বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে...
আমাদের কিছু হয়নি তা নয়। যা হয়েছে তা একবারই। ভেঙেচুরে গেলে দ্বিতীয়বার এটা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা খুবই খারাপ। একবার গিয়ে দেখলাম বনের ভেতরে কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাচা ধরনের পথ বানিয়ে দিয়েছে। সিঁড়ি বানিয়েছে। তিন বছর পর গিয়ে দেখি ওগুলো ভেঙে গেছে। কিন্তু মেরামতের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এগুলো তো ভাঙবেই। তাই বলে ঠিক করতে হবে না? পর্যটক গেলে সরকার তো এ থেকে রাজস্ব পাচ্ছে।
তাহলে ঠিক করতে সমস্যা কোথায়?
যারা দায়িত্বে থাকেন তাদের সততা প্রশ্নবিদ্ধ। যে কারণে সবসময় আমরা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকি।
সুন্দরবনে কী ধরনের কতগুলো প্রাণী আছে তার হিসাব কি আছে?
সুন্দরবনে কতটি বাঘ আছে তার সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারবে না। আমরা বলতে পারব না সুন্দরবনে কত ধরনের প্রাণী আছে, কতগুলো আছে। নামেমাত্র বাঘ গণনা করা হয়। যার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ তো এখন অনেক সচেতন?
স্বাধীনতার পর থেকে মানুষ এসব দুর্যোগের মুখে পড়ে অনেক কিছু শিখেছে, জেনেছে এবং সচেতন হয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে যেভাবে ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা সৃষ্টি হওয়া দরকার ছিল, তা হয়নি।
জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি কতটুকু?
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের দিক থেকে বিশ্ব পরিবেশের মানদ-ে প্রথম চারটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বলা হয়েছিল, ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের অর্ধেক পানির নিচে তলিয়ে যাবে।
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃত্রিম বনায়নে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু?
কিছু তো হয়েছে। দ্বীপ এলাকায় নিঝুম দ্বীপে কৃত্রিম চারণভূমি বানানো হয়েছে। সবুজ বনায়ন করা হয়েছে। হাতিয়া, ভোলার মনপুরায় বন বিভাগ কাজ করছে। কিন্তু এটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোনো ধরনের গাফিলতি চলবে না। কোনো ধরনের অনিয়ম মানা যাবে না।
বনায়ন কমে যাওয়ার কারণে জলবায়ুতে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে?
যে দেশে বনায়নের হার ১৮-২৫ শতাংশ হবে সে দেশকে আদর্শ দেশ বলা হয়। দেশের জলবায়ু নির্ভর করে গাছপালার ওপর। আকাশের সঙ্গে গাছপালার খুব ভালো সম্পর্ক আছে। ফারাক্কা বাঁধের আগে রাজশাহীতে পদ্মার পাড়ে প্রচুর বৃষ্টি হতো। তখন গাছপালা ছিল। এখন ফারাক্কা বাঁধের কারণে নদী শুকিয়ে গেছে। যখন বাঁধ খুলে দেওয়া হয় তখন পানি আসে। আবার বন্ধ করে দিলে বালুময় হয়ে যায়।
বনায়ন দেশের অর্থনীতিতে কী ধরনের অবদান রাখতে পারে?
অর্থনৈতিকভাবে বনায়ন থেকে আমরা কাঠশিল্প গড়ে তুলতে পারি। যেটা আমাদের দেশে হয়নি। ভারতে প্রচুর বনায়ন আছে। যেটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। যাকে বলে এফরেস্ট্যাশন। আর আমরা করছি ডিফরেস্ট্যাশন। সুন্দরবনসহ অন্যান্য বন থেকে গাছ কাটছি। কিন্তু রিফরেস্ট্যাশন করছি না। অর্থাৎ যে পরিমাণে গাছ কাটছি সেই পরিমাণে লাগাচ্ছি না। বন বিভাগের আপাদমস্তক দুর্নীতি। সবাই যদি সৎ না হয় তাহলে কিছুই করা যাবে না।-সাপ্তাহিক এই সময়-এর সৌজন্যে।
